তীরন্দাজ থিয়োঙ্গো সংখ্যা
নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো ২০১৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন। তিনি দর্শকদের দ্বারা উপচে-পড়া জোহানেসবার্গের একটা অডিটোরিয়ামের পোডিয়ামে এসে দাঁড়াতেই উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে বিপুল করতালি দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা দেন। তারা গলা চড়িয়ে বলতে থাকেন- নগুগি! নগুগি! নগুগি!
পঞ্চাশ বছর আগে বেরিয়েছিল Weep Not, Child; পূর্ব আফ্রিকার কোনো লেখকের ইংরেজিতে লেখা প্রথম উপন্যাস। সেই উপন্যাসের লেখক ছিলেন কেনিয়ার নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো। বিশ্বসাহিত্যের এই সুপারস্টার এরপর, বিশেষ করে জীবনের শেষ কয়েক বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু যা হয়, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য-উদারনৈতিকতাবাদের কট্টর সমালোচকের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। ইংরেজি ছেড়ে তিনি জীবনের প্রায় শুরুতেই লেখালেখি করেছেন মাতৃভাষায়, যে-ভাষার নাম কিকুয়ু। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় শিক্ষা-অর্জনের কথা বলেছেন বলে, জেলে থাকতে রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।
জোহানেসবার্গের ওই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন নাইজেরিয়া থেকে প্রকাশিত ‘দ্য ন্যাশন’ পত্রিকার সাংবাদিক-লেখক রোহিত ইনানি। নিচের সাক্ষাৎকারটি তাঁরই নেওয়া। প্রকাশিত হয়েছিল ‘দ্য ন্যাশন’ পত্রিকার ২০১৮ সালের ২ এপ্রিল সংখ্যায়।
রোহিত ইনানি : ১৯৭৭ সালে আপনি Petals of Blood প্রকাশ করেছিলেন, যা কেনিয়ার নব্য-ঔপনিবেশিক সমাজের কৃষক বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে ইংরেজিতে লেখা উপন্যাস। এর কিছুকাল পরে আপনি কিকুয়ুতে Ngaahika Ndeenda (I Will Marry When I Want – আমি যখন চাইব তখন বিয়ে করব) নামে একটি নাটক প্রকাশ করেছিলেন। আপনি Petals of Blood বইটি যাদের জন্য প্রকাশ করেছিলেন তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই কি এই নাটকটি আপনার মাতৃভাষায় লিখেছিলেন?
নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো : সত্যিই তাই। আফ্রিকার জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ মানুষ নানা ভাষায় কথা বলেন। ফলে, আপনি যখন ইংরেজিতে একটি উপন্যাস লিখবেন – তখন লেখাটি কতটা র্যাডিক্যাল তাতে কিছু আসে যায় না। সেটা যতই প্রগতিশীল রচনা হোক, অল্প কিছু মানুষের কাছে পৌঁছুবে। উপর থেকে নিচের দিকে নেমে হয়তো সামান্য কিছু পাঠককে ছোঁবে।
ইনানি : উপন্যাসটি প্রকাশের পর আপনি কি কোনো বিপ্লব ঘটে যাবে বলে আশা করেছিলেন?
থিয়োঙ্গো : না, কখনই না। শিল্প কখনও উস্কানি দেয় না। শিল্প কল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত। দমনমূলক শাসনব্যবস্থার সমস্যা হলো, সেই শাসন শিল্পকে কল্পনাবঞ্চিত রাখতে চায়। তার ভিন্ন কোনো ভবিষ্যৎ যে হতে পারে, সেই কল্পিত পরিসরের কথা ভাবতে পারে না। তারা বলতে চায়, তারা যে পৃথিবীর কথা বলছে, সেটাই সম্ভাব্য সেরা পৃথিবী। ইংরেজিতে লিখে, অথবা যদি নিশ্চিত করেন যে সাহিত্য শুধু ইংরেজিতে রচিত হয়, তাহলে আপনি অধিকাংশ মানুষকে কল্পনার দিক থেকে ক্ষুধার্ত রেখে দেবেন।
ইনানি : ১৯৭৮ সালে আপনি ‘কামিতি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা কারাগারে’ বন্দি থাকার সময় আপনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা Davil on the Cross বইটি শুধু টয়লেট পেপারে কিকুয়ু ভাষায় লিখে গেছেন। একটা আস্ত বই টয়লেট পেপারে লেখা কতটা কঠিন ছিল?
থিয়োঙ্গো : I Will Marry When I Want বইটির জন্য আমাকে কারাগারে পাঠানো হয়ে, নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল কিকুয়ু ভাষায় এবং এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন কৃষকরা। কারাগারে থাকতে ভাষার প্রশ্নটি আমি খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে থাকি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, উপনিবেশবাদের ইতিহাসের দিকে তাকালে, উপনিবেশবাদীরা কেবল তাদের ভাষাকে চাপিয়ে দেয়নি, বরং তারা উপনিবেশিতদের ভাষাগুলোকে অবজ্ঞা করেছে, দমন করেছে। আমাদের ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাই ছিল ইংরেজি ভাষা শেখার শর্ত আর তা উপনিবেশ-পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিল। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যেহেতু আমাকে একটি জাতীয় ভাষায় লেখালেখির জন্য কারাগারে পাঠানো হয়েছে আর আফ্রিকার একটা সরকার আমাকে আটক রেখেছে, তাই প্রতিরোধের অংশ হিসেবে আমি সেই ভাষাতেই লিখব যে-ভাষা আমার কারাবাসের কারণ হয়ে উঠেছিল।
ইনানি : আপনি ভাষাকে ‘যুদ্ধক্ষেত্র’ আর নিজেকে ‘ভাষাযোদ্ধা’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিষয়টা নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলবেন?
থিয়োঙ্গো : ব্রিটিশদের সঙ্গে মিলিয়ে আইরিশদের দেখুন, অথবা ভাবুন আমেরিকার আদিবাসীদের ভাষাগুলোকে কীভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছিল। আফ্রিকায়, অবশ্যই, আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছিল। জাপান তাদের ভাষা কোরিয়দের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। আপনি আধুনিক উপনিবেশবাদের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন, উপনিবেশিতদের ভাষার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই উপনিবেশবাদের ভিত্তি রচিত হয়েছে। সুতরাং এটি তো একটি যুদ্ধক্ষেত্রই। ভারতের ক্ষেত্রে দেখুন, [ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এবং রাজনীতিবিদ টমাস ব্যাবিংটন] মেকলে ইংরেজির উপর নির্ভরশীল ভারতীয় একটি শ্রেণি তৈরির বিষয়ে নির্মমভাবে সৎ ছিলেন। ইংরেজরা চেয়েছিল এই ভারতীয় শ্রেণি বাদবাকি ভারতীয় মানুষের শাসকের ভূমিকা পালন করবে। ঔপনিবেশিক শাসন আর সেই শাসনকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভাষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। কারণ ভাষাই সম্ভবত পারে মধ্যবিত্তের মনকে আবদ্ধ রাখতে।
ইনানি : আপনি কি মনে করেন, ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ মনে-করা মুক্ত-উন্নত সমাজের একজন লেখকের তুলনায় উপনিবেশ-উত্তর সমাজের একজন লেখকের রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং ঐতিহাসিক অবিচার সম্পর্কে লেখালিখি করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে?
থিয়োঙ্গো : কোনো লেখক যদি বলেন, ‘ওহ্! আমি তো রাজনীতি নিয়ে লিখি না’ – এটা আমি বিশ্বাস করি না। আসলে, লেখক রাজনৈতিক লেখাই লেখেন। কেননা, তিনি সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে কোনো না কোনো বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন। লেখকের সচেতন থাকা উচিত যে, কোনো লেখক নিরপেক্ষ নন। লেখকমাত্রই নির্দিষ্ট ইতিহাস ও শ্রেণি-অবস্থান থেকে সৃষ্টি হয়। ইতিহাসের আঘাত প্রতিটি লেখককেই ক্ষত-বিক্ষত করে।


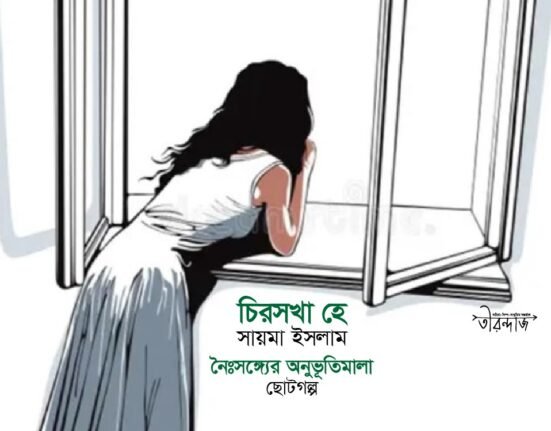

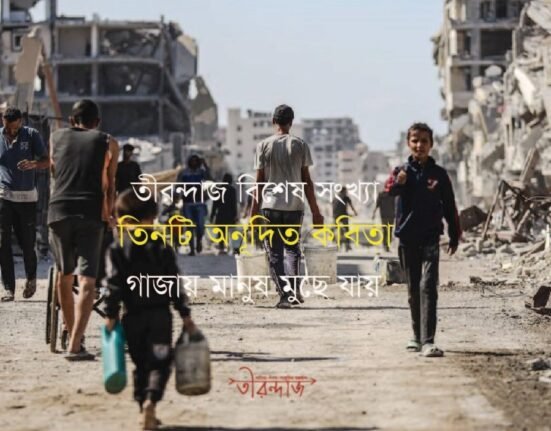
Leave feedback about this