নারীর স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ | শেষের দিনগুলি | যোবায়দা মির্যা
১৯৭১ সনের পনরই ডিসেম্বর আমার জীবনের একটি অত্যন্ত জটিল রকমের গুরুত্বপূর্ণ দিন। শুধু আমার বলি কেন, প্রত্যেক বাংলাদেশির জন্যেই এটি একটি বিশেষ দিন। এক টানা নয়মাস ধরে যত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-আনন্দ-বিষাদের ঠাসবুনুনি। সকলেরই অভিজ্ঞতা রকমারি। কখন কি হয়, কখন কি হয়, বসে বসে শুধু মুহূর্ত গোনা। কিছু না-হওয়াটা আরো বেশি দম-বন্ধ-করা রকমের মারাত্মক। এ যাবত অনেক বইই বেরিয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার। আমার মনে হয় প্রায় সবগুলোই পড়েছি। মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে গেছে ‘একাত্তরের দিনগুলি’, ‘নিষিদ্ধ লোবান’, ‘জীবন আমার বোন’… নূতনত্বের দিক দিয়ে প্রত্যেকটি আলাদা – বানানো গল্প নয়। এগুলোর সাথে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নোট মেলাতে বসলে তাতেও কিছুটা অভিনবত্ব নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।
মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে – মুক্তিবাহিনী ঢাকায় ঢুকে পড়েছে। এখানে ওখানে খণ্ডযুদ্ধ চলছে স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে। স্বাধীন বাংলা রেডিও থেকে কিছুক্ষণ পর পরই ঘোষণা হচ্ছে নিয়াজীর প্রতি আত্মসমর্পণের ডাক। তখন জয়বাংলা রেডিও শোনা নিষেধ। সবাই শোনে, কেউ বলে না। সবাই ভাবে, ‘আমি যে-খবর জানি তা বুঝি আর কেউ জানে না!’ রাস্তার ধারে বাড়ি। প্রকাণ্ড গ্রুনডিগ রেডিওটার ভ্যাড়ভ্যাড়ে আওয়াজ। পূরোমাত্রায় ঢাকা বেতার কেন্দ্রে লাগিয়ে দিয়ে ভেতরের দিকের ঘরে চুপি চুপি কান লাগিয়ে শুনি ছোট সোনি ট্র্যাঞ্জিস্টারটা। এটার আওয়াজ হাল্কা কিন্তু স্পষ্ট। সারাক্ষণই কেউ না কেউ কান পেতে বসে আছে আর উল্লেখযোগ্য খবর হলেই সবাইকে ডেকে শোনাচ্ছে চরমপত্র, অরোরার গলা, মেজর জিয়ার গলা। বাড়িময় প্রচণ্ড উত্তেজনা। নিঃশব্দে ইশারা, ফিসফাস – সবাই যেন কথা বলতে ভুলে গেছে। প্রত্যেকের চোখে আতঙ্ক আর জিজ্ঞাসা। পুরো নয়টি মাস প্রায় একভাবেই কেটেছে। হানাদার বাহিনীর গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করা, অধিবাসীদের সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে একসাথে গুলি করার কাহিনী, মেয়েদের ওপর অত্যাচার, লুটতরাজ, খুনখারাবীর কত রকম কীর্তি কানে আসে – গুজব বলে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না কোনটাই। আশেপাশে অনেক আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশী গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে কত নাজেহাল হয়ে, দেউলে হয়ে ফেরত এসেছেন। মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বারীণ মজুমদার এক সন্তান হারিয়ে ফিরেছেন। কোথাও নিরাপত্তা নেই। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর। আমরাও দেশের বাড়িতে চলে যাবো কি না চিন্তা করছি এমন সময় আমারই এক দেবর গ্রাম থেকে ঢাকায় এলেন। তিনি বললেন, ‘ভাবী, যাবেন কোথা? যেখানে আছেন এখানেই থাকেন। যা থাকে কপালে। এখন বেঁচে থাকাটাই অ্যাক্সিডেন্ট, মরাটাই স্বাভাবিক। দৈবাৎ যদি পাকবাহিনীর হাত থেকে বেঁচেও যান, আমাদের খাঁটি দেশীয় চোরডাকাতের হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। ভোগান্তির একশেষ হবে!
আমাদের গ্রামে খান সেনারা এসেছিল। আমি সেখান থেকেই আসছি। ওরা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে এনে মাঠের ধারে লাইন করে দাঁড় করালো। সামনাসামনি সেই লাইন বরাবর এক দল অস্ত্রধারী সৈন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে শুধু মাত্র ‘ফায়ার’ অর্ডারের জন্যে। আমাদের সকলেরই চোখে পানি, হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, কারো মুখে কথা সরছে না, মনে মনে ইষ্ট নাম জপ করেছি কি না বলতে পারি না, সবাই স্তব্ধ। হঠাৎ সজোরে কান ফাটানো অর্ডার এলো, ‘স্টপ’। হতবুদ্ধি হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ঘাতকরা উদ্যত অস্ত্র নামিয়ে দলপতির দিকে অবাক চোখে তাকালো, ‘ব্যাপার কি!’ আমরা চেয়ে দেখি, সেই হিংস্র লোকটারও চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় পানি গড়িয়ে পড়ছে, আমাদের চেয়েও বেশি। ধরা গলায় দলপতি বললো, ‘তোমরা যে যার বাড়ি ফিরে যাও। আর কোন সৈন্যদল তোমাদের বিরক্ত করবে না।’ অবিশ্বাস্য নাটকীয় ব্যাপার। বাড়িঘর কোথায়? সব তো আগেই পুড়িয়ে শেষ করেছে। আমরা তো বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি, দলপতি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, ‘আপাতত কোন রকমে বাড়িঘর মেরামত করে নাও। ঐ যে তোমাদের লাইনের শেষে একটি মেয়ে সমানে চোখের পানি মুছছে, ঠিক অমনি একটি বোন আছে আমার, মুলুকে রেখে এসেছি। ওর দিকে চোখ পড়তেই আমি আর ফায়ার অর্ডার দিতে পারলাম না।’
‘ভাবী, বাড়িঘর, জিনিসপত্র সব গেছে। তবু একটা এতিম মিসকিন, আধপাগলা মেয়ের জন্যে আমরা প্রাণে বেঁচে গেলাম। অলৌকিক ঘটনা! জীবন আর মরণের মাঝে মাত্র চুল পরিমাণ ব্যবধান। কয়েকটা মিনিট আমাদের কেটেছে হাজার বছরের মরণ যন্ত্রণায়! কেমন যে লেগেছে, মুখে বলে এই সব কথা বোঝাতে পারবো না।’
বিবরণ শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিলাম। আর যাবোই বা কোথায়? প্রথমে শোনা গেল, ওরা নাকি মুসলমানদের মারছে না। সেই ভরসায় বাড়িতে ঢুকতেই চোখে পড়বে এমন জায়গায় আল্লাহ্, রসুলের নাম, দোয়াদরুদ লিখে রাখলেন অনেকে। কিছুতেই কিছু হয় না। এই ঢাকা শহরেই বাড়ি বাড়ি ঢুকে অত্যাচারের খবর ক্রমশ বেড়েই চললো। শুনলাম, এক বাড়ির পাঁচটি সোমত্ত মেয়ে জিপে উঠিয়ে নিয়ে যাবার সময় তাদের বৃদ্ধা মা কোরাণ শরীফ হাতে করে দোহাই পাড়তে পাড়তে ওদের পিছু পিছু ছুটে সেই জিপের পথ আগলাতে গেলেন; জানোয়াররা তাঁকে বুটসুদ্ধ পায়ে লাথি মেরে ফেলে কোরাণ শরীফের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল বিনা দ্বিধায়। হতভাগিনী মায়ের দিকে ফিরেও তাকালো না। ওরা তো ঘোরতর মুসলমান, এ দেশে কাফের নিধন করতে এসেছে!
আরো কত লোমহর্ষক গল্প মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। তবু এতটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হতো না। কারণ নিজের ঘরেও যে তিন-তিনটে সেয়ানা মেয়ে আর একটি সদ্য বিবাহিতা ছেলের বৌ। আবার শুনি ওদের কাছে বয়সের কোন বাছবিচার নেই। ঘরে বসেই খবর পেতাম, আজ একে ধরে নিয়ে গেল, কাল ওকে ধরে নিয়ে গেল। দশ থেকে ষাট পর্যন্ত সবই মেয়ে! ভয়ে আধমরা হয়ে দিন গুনছি, আহা! কবে ঐ সবুজের মধ্যে মানচিত্র আঁকা বাংলাদেশের ফ্ল্যাগটা ওড়াতে পারবো! সেটা মাত্র কয়েকদিনই উড়িয়েছি ছাত্রদের উৎসাহের চোটে। তারপর আবার হানাদারদের হুঙ্কারে জড়সড় হয়ে ভাঁজ করে অতি অন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছি তোষক জাজিমের কোন ফাঁকে গুঁজে।
ওদের নির্যাতনের পদ্ধতি শুনে কণ্টকিত হয়ে থাকতাম। আমাদের পরিচিত একটি ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল। সে তাদের বাড়ির বড় ছেলে। তার কাছেই শুনেছি। পুরো আর্মি ক্যাম্পের সব লোকজন জড় করে তাদের সামনে এই সব নিরীহ বাচ্চা ছেলেদের টর্চার করাটা এক রকম আনন্দ উৎসব ছিল তাদের জন্যে এবং এটা তাদের প্রাত্যহিক রুটিনভুক্ত কাজ। এই ছেলেটিকে একদিন মাথা থেকে পা পর্যন্ত পিটাতে পিটাতে অজ্ঞান করে ফেললো। তারপর চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরলে আবার পিটুনি, বুটসুদ্ধ পায়ের অনবরত লাথি। এমনি করে শেষ পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় শরীরের মাংসগুলো কিমা হয়ে চারিদিকে ছিটকে গিয়ে ওদের গায়ে মুখে পড়ছে আর পিশাচদের সে কী উল্লাস আর অট্টহাসির ঘটা! বেচারাকে অনেক কায়দা কৌশল করে আত্মীয়-স্বজনরা ওদের খপ্পর থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। বাপ-মা তাতেই খুশি। ছেলেটা অনেক দিন পর্যন্ত চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, অন্যমনস্ক হয়ে কী যে ভাবতো তা সে-ই জানে। মাঝে মাঝে এমন ফ্যালফ্যাল করে তাকাতো যেন এ জগতেই নেই সে। শিক্ষা বিভাগের লোকের কী সুন্দর, বুদ্ধিমান, সম্ভাবনাময় ছেলে। বাপমায়ের চোখের ওপর খুব ধীরে ধীরে অনেক দিন লাগিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে এখন। তবু আগের মতো কি আর হয়! ওর অন্য সব ভাইরা বেশ ভাল ভাল চাকরি করছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে আছে। কিন্তু ও বেচারির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিছুদিন হয় বাবা গত হয়েছেন। মা এখনো আছেন, কিন্তু মনে সুখ কই? সন্তানকে এমন জীবনন্মৃত দেখতে মায়ের কতখানি মনের জোরের দরকার!
কত রকম ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, স্বামী, ছেলে, মেয়ে অকালে হারিয়ে গেছে কত তার কতটুকুই বা লেখাজোখা আছে? আমারই এক ছাত্রীর স্বামী সেই যে অফিসে গেছে আজও ফেরেনি। তার ছেলেমেয়েরা আর কাঁদাকাটি করে না বটে, তবু আশা ছাড়েনি, ‘বাবা কবে আসবে? আসবে তো?’ এই প্রশ্নে ওর মনের পুরোনো ক্ষত হঠাৎ খোঁচা লেগে আবার টাটকা তাজা রক্ত ঝরায়। ও ভাবে, ‘সত্যিই আসবে কি? আচ্ছা এত দিন পরে এলে আমি কি তাকে চিনতে পারবো? বদলে যায়নি তো?’
এখানে-ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনের খবর জোরদার হয়ে উঠতে লাগলো ক্রমশ। বেশ কয়েকটা ঘটনা এই ধানমন্ডিতেই ঘটলো, আমার বাড়ির কাছেই। একদিন দোতলার বারান্দায় বসে ইপিআর-এর কোনায় দুটো প্লেনের সামনা সামনি যুদ্ধ দেখছিলাম। হঠাৎ একটা প্লেনে আগুন লেগে গেল, পাইলট প্যারাসুটে ঝুলতে ঝুলতে নেমে পড়লো। আশেপাশের ছেলেরা ছুটে গিয়ে খবর আনলো, এক অল্পবয়সী ভুটানি পাইলট সারেন্ডার করেছে। মন খারাপ হয়ে গেল, এখন ইণ্ডিয়াই আমাদের পরম বন্ধু – অথচ ছ’বছর আগে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ওরা ছিল বিপক্ষ। সে সময় আমি বিলেতে – পুবে বাঙালিরা সারাক্ষণ বসে রেডিও টেলিভিশন খুলে খবর শুনি আর ভাবি, বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, কিছুই বুঝি আর নেই…। তারপর যুদ্ধ থামে। বিজয়-উৎসব হয় পাকিস্তান হাইকমিশনে আবার ইণ্ডিয়ান হাইকমিশনেও। কে জিতলো, কে হারলো বোঝা গেল না। পরে ঢাকার চিঠিপত্র পেয়ে বুঝলাম সব ঠিকঠাক আছে। কাজেই হারজিতের প্রশ্নটা চাপা পড়েই রইলো। কিন্তু এবার ব্যাপারটা একদম অন্য রকম। প্লেন উড়ছে, স্ট্রেফিং হচ্ছে, বাতাসে খবর উড়ে আসছে – এই এসে পড়লো বলে রায়ের বাজারের দিক দিয়ে নদী পথে। এই শুনি রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, এই সেগুনবাগিচায় বাপের বাড়ির পাড়ায়, হঠাৎ শুনি ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে ড. হাসান জামানের ফ্ল্যাটে… মনে মনে বাহবা করি, ওরা কী করে এমন মোক্ষম টার্গেটগুলো চিহ্নিত করে। বুকের ভেতর কিন্তু দুরুদুরু করছে কখন কী হয়। বিদেশে বসে যুদ্ধের খবর শোনা আর যুদ্ধের সময় দেশের মধ্যে চোখ, কান খুলে মুখ বুজে আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। ক্রমে যুদ্ধ আরো কাছে ধানমন্ডি, নিউমার্কেটে এসে পড়লো। আকাশে প্লেন থেকে নানা রকম হ্যাণ্ডবিল, প্যামফ্লেট ছড়িয়ে পড়ছে উঠোনময়। বাচ্চারা দারুণ উল্লাসে কুড়িয়ে আনছে যে যতটা পারে – ওরাই সুখে আছে নিজেদের নির্মল আনন্দ নিয়ে।
ঘরে কিছু পাইকারি হারে ডিম-চাল-ডাল-আলুর জোগাড় রেখেছি। বাজারের নিশ্চয়তা নেই। কখনো কারফিউ পড়ছে ক্রমাগত আটচল্লিশ ঘণ্টা, বাহাত্তর ঘণ্টার জন্যে। মাঝে মাত্র দুতিন ঘণ্টার বিরতি। ওর মধ্যেই ছুটোছুটি করে বাজারের চেষ্টা করে – রায়েরবাজার, মোহম্মদপুর, নিউমার্কেট, হাতিরপুল – মাছতরকারি কখনো কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়, কখনো যায় না। তা ছাড়া যিনি যাবেন তাকে প্রাণটি হাতে করে শেষবিদায় নিয়ে যেতে হয়, না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি নেই কারও।
একদিন রাত দুপুরে-আড়াইটা/তিনটে হবে – হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বাড়িঘর কাঁপিয়ে বিস্ফোরণ। সকালে জানা গেল, আহ্ হা! সেইম সাইড হয়ে গেছে! তেজগাঁয় এক এতিমখানার ওপর বোমা বর্ষণ করেছে পাক আর্মি। রাস্তায় ট্যাংক নেমেছে, ভারী গোলাবারুদের সমারোহ! যুদ্ধ ক্রমশই এগিয়ে এসে ঘনীভূত হচ্ছে ধানমন্ডির দিকে – এ যেন মরিয়া হয়ে শেষ কামড় বসানো!
অবস্থা এমন দাঁড়ালো, প্রতিবেশীদের মধ্যে নিজেরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি না। থাকি ধানমন্ডি পনের নম্বরের মাঝামাঝি। এ রাস্তাটা অনেক লম্বা – এডভোকেট মোজাম্মেল হক সাহেবের বাড়ির উত্তর দিক দিয়ে আরম্ভ হয়ে সোজা চলে গেছে একদম পশ্চিম প্রান্তে রায়ের বাজার পর্যন্ত। এখন অবশ্য নম্বরটা পাল্টে হয়েছে ৮/এ। এর দুধারের বাসিন্দাদের সমীক্ষা নিলে দেখা যাবে এখানে ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে, সংসদ-সদস্য, ইত্যাদি সব রকম পেশাজীবী বাস করেন। এককথায় এখানে যেন গোটা সমাজটার একটা ক্রসসেকশন পাওয়া যাবে জাতিধর্ম নির্বিশেষে। দু’ একজনের নাম করলে আমার বক্তব্যটা আরেকটু পরিষ্কার হবে। এ রাস্তায় পড়তেই প্রথম বাড়ি এডভোকেট মোজাম্মেল হক সাহেবের, নাম তো আগেই করেছি। তারপর এখান থেকে বরাবর পশ্চিমে রায়ের বাজারের দিকে চলতে থাকলে অনেক নামজাদা লোকের বাড়ি পড়বে ডাইনে-বাঁয়ে। যেমন, চোখের ডাক্তার ওয়াদুদ সাহেব, শিক্ষাবিদ বোরহানউদ্দিন সাহেব, হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের কর্মকর্তা আরশাদ সাহেব, বিশিষ্ট সরকারি অফিসার শাহজাহান ভূঁইয়া, সার্জন ডা. আছিরুদ্দিন, কর্ণেল মতিয়ূর রহমান, সংসদ সদস্যা মিসেস খালেদা হাবীব, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী, এডভোকেট মির্জা গোলাম হাফিজ ইত্যাদি রথী-মহারথীর মাঝে আমি এক চুনোপুঁটি ইডেন কলেজের অধ্যাপিকা। আমার বাড়ির দক্ষিণে ড. আশরাফ সিদ্দিকীর বাড়ি, মাঝে শুধু একটা পাঁচ ইঞ্চি চওড়া দেয়াল। এঁদের অধিকাংশ বাড়ির সাথেই প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের কমবেশি আসা-যাওয়া আগে থেকেই ছিল, তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের সহপাঠী ছিল প্রায় বাড়িতেই। এত যে আলাপ, আসা-যাওয়া ক্রমে কমে এলো। দৈবাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলে, ‘কী, কেমন আছেন?’ এই পর্যন্তই। কে যে পাকিস্তানি আর কে যে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক, বোঝা মুশকিল। পাড়ার মধ্যে একমাত্র আরশাদ সাহেবের ছেলেমেয়েরা আমার ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশা করতো অসঙ্কোচে। কর্ণেল মতিয়ূর রহমান সাহেবের বাড়ির সামনে রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে আমানুল্লাহ্ সাহেবের বাড়ি। তাঁর স্ত্রী ফরিদা ওরফে বীথি এককালের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ফিরোজা বারী মালিকের মেয়ে। পারিবারিক সূত্রে এদের সাথে আমাদের বহুদিনের আলাপ। তবুও ঠিক ঐ সময়টায় কেমন একটা থমকে থেমে যাওয়া ভাব।
আমার বাড়িতে প্রতিবেশীদের হরহামেশা না আসার একটা সঙ্গত কারণ ছিল অবশ্যই। সে সময় সিলেটের এক ইঞ্জিনিয়ার অজয় সিন্হা আমার একতলায় ভাড়া ছিলেন। তার ভাইবোনেরা এখানে থেকে কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে পড়তো। সেই সুবাদে সিলেটের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে এসে বেড়িয়ে গেছেন। ইংরেজির অধ্যাপক কৃষ্ণবাবু তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছেন। রাখী চক্রবর্তী, আরতি ধরের গান আমরা বাড়িতে বসেই শুনেছি। তা ছাড়া ভারতীয় হাইকমিশনের অফিসাররা অনেক সময়ই আসতেন ওদের কাছে। ধর্মগত ব্যবধানের কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হয়ত তাতেই পাক-বাহিনীর চোখে পড়বার ভয় পেয়েছিল কেউ কেউ… এমন সময় পাক আর্মির ক্যাপ্টেন ফারুক এসে পাট্টা গাড়লেন এ পাড়ায়, খুব দহরম-মহরম। প্রত্যেক দিন আর্মি জিপের আনাগোনা টের পেতাম। মাঝে মাঝে সেপাই-সান্ত্রীরা পজিশন নিয়ে তাক করে বসে আছে। ব্যাপার কি? পাড়ার বেশ কয়েকটা বাড়িতেই ক্যাপ্টেন ফারুক বন্ধুভাবে আসতো অষ্টপ্রহর। প্রতিবেশী এক মহিলা একদিন গল্পচ্ছলে বেশ জোর গলায়ই বললেন, ‘আমরা ক্যাপ্টেন ফারুককে খাইয়েদাইয়ে হাত করে রেখেছি বলেই না আজ পর্যন্ত এ পাড়ায় কোন অঘটন ঘটে নাই। নইলে আর্মির যন্ত্রণায় মেয়েদের নিয়ে এখানে বাস করাই কঠিন হতো। চারিদিকে যে সব কেচ্ছা শোনা যাচ্ছে ওদের উৎপাতের!’ যেসব বাড়িতে এই ক্যাপ্টেন সাহেব যেতেন তারা সদাই প্রভুর তুষ্টির জন্যে সচেষ্ট। কেউ পাকিস্তানের পায়েন্দায়েশের জন্যে মিলাদ পড়িয়ে মোনাজাত করছে, কেউ গেট বরাবর চেয়ার টেবিল সাজিয়ে ক্যাপ্টেন সাহেবকে ঘিরে বসে মনের আনন্দে চা-নাস্তা খেতো, সেই সঙ্গে হাসি-তামাশা-গল্প চলতো হরদম।
আরো একটা কারণে আমরা প্রায় একঘরে হয়ে পড়েছিলাম সেই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে। পাকবাহিনী শেখ মুজিবের পরিবার পরিজনদের এনে আটকে রেখেছিল। ওদেরকে শুধু আটকে রাখা ছাড়া আর কোন কষ্ট দেয়না। প্রচুর ভাল ভাল খাবার এনে দেয়। নিজেদের পছন্দমত রান্না করে খাবার জন্যে বাজারের সেরা চাল-ডাল-মাছ-মাংস-তরকারি-তেল-ঘি-মসলা সব এনে দেয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কিন্তু সকলেরই মন খারাপ, কার রান্না কে রাঁধে! একদিন ওদের আম্মা রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে বেশ পোলাও-কোর্মা, আরো অনেক কিছু রান্না করেছিলেন। ওরা কেউই খেতে পারেনি, রাসেল নিজেও না। এইসব কথা বলতে বলতে রেহানা কেঁদে ভাসাতো। বিকেল পার হলে ওরা আবার ফিরে যেতো নিজেদের পিঞ্জিরায়। পাড়ার আঠারো নম্বর রোডের একটা লাল রঙের বাড়িতে। আমাদের পরের সমান্তরাল রাস্তাটাই আঠারো নম্বর। আ¬মাদের বাড়ি থেকে একটা কাক সোজা উত্তর দিকে উড়ে যেতে গেলে প্রথমে পড়বে ডা. আছিরুদ্দিনের বাড়ি, তারপর আঠারো নম্বর রোডের ওপর দক্ষিণমুখো লাল দোতলা বাড়িটা। সেটা আমাদের এখান থেকে দেখা যায় না বটে, তবে ওখানকার গার্ডরা ভারী তুখোড়, ছাদে উঠে চারিদিকের সব কটা বাড়ির ওপর খবরদারি করতো। ওদের বন্দীদের নাম দিয়েছিল, ‘আস্লী চিড়িয়া’। তারা এই চিড়িয়াদের কড়া পাহারা দিত। শুধু শেখ সাহেবের ছোট ভাই, ছোট মেয়ে রেহানা ও ছোট ছেলে রাসেলকে মাঝে মাঝে কি জানি কেন বেরুতে দিত সারাদিনের জন্যে। হয়ত নজর রাখতো চিড়িয়া উড়ে কত দূরে যায়। বেশিদূর যেতোনা ওরা। দৌড় আমাদের বাড়ি পর্যন্তই। এমন মনমরা, নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল ওরা! রেহানার চাচা আমাদের বারান্দার কোণায় একটা বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকতেন। রেহানা তাকে বলতো, ‘কোথাও গিয়ে ঘুরে এলে মনটা ভাল লাগবে।’ তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, ‘নারে মা, কোথায় ঘুরতে গিয়ে কার বিপদ ডেকে আনবো? আমাদের পেছনে ফেউ লেগেই আছে নিশ্চয়। এখানে আসাটাও ঠিক হচ্ছে না।’ এ কথায় সায় দিয়ে চলে যেতেও পারতো না রেহানা। ও শুক্লার সাথে পড়তো, দারুণ বন্ধুত্ব দুজনে। ততক্ষণে অনর্গল গল্প শুরু হয়ে যেতো দুই বন্ধুতে। রাসেল অত্যন্ত দুরন্ত ছেলে, ওর বয়সের উপযোগী। রেহানা তাকে ধরে রাখতে পারতো না। একটু ফাঁক পেলেই দে-ছুট, উঠোনময় সে কী ছুটোছুটি! শুক্লা, রেহানা, ওর চাচা তিনজনে মিলে তিন দিক থেকে তাড়িয়ে কত কষ্টে পাকড়াও করতো ওকে। ওর কোন খেলার সাথী নেই, সারাক্ষণ ঘরে বন্দী থেকে থেকে ও আরো খ্যাপার মতো হয়ে গেছে। সবচেয়ে ওরা মন খারাপ করতো কিছু খেতে দিলে।
পাড়ার লোকে বলতো, আমাদের নাকি পাখনা গজিয়েছে। কোন্ দিন আর্মি এসে হানা দেয় তার ঠিক নেই। পাড়ার মধ্যে একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড না বাধালে আর চলছে না! মনে মনে ভাবি, ওরা কোথায় যাবে? কী করেই বা মানা করি আসতে! কপালে যা আছে হবে, কী আর করা! মুখে কথা বলি না। রেহানাদের আসা-যাওয়া নিয়মিত হতে থাকলো।
সেদিন কলেজে তেমন কাজ ছিল না। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রহসন দিন কয়েক আগে শেষ হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় না গেলেও চলতো। যুদ্ধের সময় বলে কড়া হুকুম, হাজিরা দিতেই হবে কাজ থাক বা না থাক। সময় মতো ইডেন কলেজের পথে রওয়ানা হলাম রিক্সায়। মাথার ওপর অনেক প্লেন উড়ছে। কোথেকে এক বুলেট এসে রিক্সার মধ্যে. আমার পায়ের ঠিক দেড় ইঞ্চি পাশে পড়েই ছিটকে রাস্তার ওপারে গাছটার গোড়ায় গিয়ে পড়লো। ঐখানেই রিক্সাটা রেখে চালক রাস্তা ক্রস করে বুলেটটা কুড়িয়ে আনলো।
‘দ্যাখছেন নি? পেলেনের থন ফালাইছে।’ দেখেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সর্বনাশ! একটুর জন্যে পায়ের পাতাটা ফুটো হয়ে যায়নি। আতঙ্কে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলাম। কোনোরকমে হাজিরা দিয়েই বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু না বলে ড্রইংরুমে মাদুর পেতে বেশ কম্বল মুড়ি দিয়ে পাটিসাপটা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে মিলিটারি অফিসার দুজন এসেছিল আমাদের বাড়ি তল্লাসী করতে। ওরা ঢুকেই সোজা ওপরে উঠে এসেছে। ড্রইংরুমে আমাকে অমন মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে বললো, ‘থাক, একে ডেকে কাজ নেই, অন্য ঘরগুলো দেখে আসি আগে।’ প্রথমেই ঢুকলো মেয়েদের ঘরে – তিন কন্যার তিনটে খাট আর তিনটে ট্রাংক। ওদের কাপড় চোপড় গহনাগাঁটি যা কিছু সম্পত্তি সব যার যার ট্রাংকে। প্রথম অফিসারের হাতে একটা বেতের ছড়ি, অন্যজনের কাঁধে বেয়নেট। ছড়ি দিয়ে একটা ট্রাংক দেখিয়ে খুলতে বললো। অফিসার ছড়ি দিয়ে কাপড়চোপড় নেড়েচেড়ে তল-ওপর করে উল্টেপাল্টে রেখে ছেলের ঘরের দিকে চললো। ছেলে একটু আগে কলেজ থেকে ফিরে গোসল করতে ঢুকেছে। বৌমাকে বললো খাটের তলা থেকে সুটকেসটা বের করে খুলতে। ওতে ঠাসা ছিল ওর বিয়ের যত শাড়ি-গহনা। হাত দিয়ে কিছুই ছুঁলো না ওরা, শুধু ছড়ির আগা দিয়ে আলগোছে একটু নেড়ে সুটকেস বন্ধ করতে বলে আরো দুটো ঘর পার হয়ে রান্নাঘরের পাশের ঘরে গিয়ে উঠলো। ও ঘরে যত রাজ্যের বইপত্রের গাদি প্রায় ছাদ সমান। একপাশে একটা খাটে থাকতো আমাদের আধ-পাগলা বুড়ি ঝি। সে বাইরের লোকজন দেখে ঘোমটা টেনে পেছন ফিরে বসেই রইলো খাটের ওপর। অফিসার দরজার কাছ থেকে একবার তাকিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখে নিয়ে বললো, ‘এখানে এত বোঝাই মাল কেন? কিছু কিছু সরিয়ে হালকা করে রাখবেন, কাল আবার আসবো।’ ড্রইংরুমে ঢুকলো না। আমি তখনো আরামসে ঘুমুচ্ছি। আমার কর্তার সাথে কথা বলতে বলতে সিঁড়িতে ভারী বুটের শব্দ তুলে যখন ওরা নেমে যাচ্ছে তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো। ভাগ্যি ভালো যে বৌমা কিংবা মেয়েরা কেউ ভয় পায়নি। আমি হলে কিন্তু ভীষণ ঘাবড়ে যেতাম। একদিনে এত সারপ্রাইজ আমার সহ্য হতো না।
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কর্তার সাথে ওদের যে সব কথা হলো তা আরো মজাদার। ‘নিচের তলায় কারা থাকে?’ ‘আমাদেরই এক আত্মীয়।’ এ পর্যন্ত বেশ খোশ মেজাজেই কথাবার্তা হচ্ছিল উর্দুতে। নিচের লোকেরা তখনও অফিস-আদালত-কলেজ থেকে ফেরেনি। দরজায় তালা দিয়ে ওদের চাকরটা বাজারে গেছে। এরাও সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছেছে আর চাকরটাও বাজার থেকে ফিরে কেবল তালার মধ্যে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলছে। চট করে ঘটনার মোড় ফিরে গেল। ‘অ্যাই, তোর নাম কি রে?’ ও বেচারা এমন ভড়কে গেল! আর্মি সাজপোশাক, বেয়নেট দেখে তোল্লাতে তোল্লাতে নিজের নাম, বাবুর নাম, সব বলে ফেললো। হতভাগাকে দিন পনর থেকে মুসলমান নাম আরব আলী শেখানো হয়েছে। তাই কি আর মনে থাকে? সময় মতো দিলো মাটি করে সব! অফিসার এবার আমার কর্তাকে নিয়ে পড়লো : ‘এরা তো দেখছি হিন্দু। আপনি না বলেছিলেন আপনার আত্মীয়? মিথ্যা কথা বলেছেন?’ ‘মিথ্যা কেন হতে যাবে? বৈবাহিক সম্পর্কে আত্মীয় হতেই তো পারে।’
‘আপনাদের রানা লিয়াকত আলী কি হিন্দু ছিলেন না? অরুণা আসফ আলী?’ রাগে ফেটে পড়লো খান সাহেব। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চাকরকে বললো, ‘এ বাঙালের বাকোয়াস শোনার মতো এত সময় আমার নেই। এরা সব গেছে কোথায়? কাল সকালে বাসায় থাকতে বলবে।’ তারপর আমার কর্তার দিকে ফিরে চোখমুখ লাল করে ছড়ি নাচাতে নাচাতে শাসালো, ‘কাল ভোরেই আসছি। মিথ্যা কথা যদি হয়, তবে সব কটাকে এক সাথে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করবো। মনে থাকে যেন।’ বলতে বলতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। কর্তামশাইয়ের তো অবস্থা কাহিল!
ওদিকে আরেক কাণ্ড। এরা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে ঠিক সেই সময় আমার ছেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই দেখে অজয়বাবুরা দুইভাই নিশ্চিন্ত মনে হেলেদুলে বাড়ি ফিরছেন। ও তো আতঙ্কে চীৎকার করতেও পারছে না, চার হাত-পা নেড়ে অনেক মুশকিলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইশারায় ফিরে যেতে বললো। তারা তখনই ঘুরে আরশাদ সাহেবের বাড়ি গিয়ে ওঠাতে রক্ষা। আমাদের বাড়িতে মিলিটারি জিপের আগমন ওরা আগেই টের পেয়েছিল, ওদের ছেলেরা ওদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিলিটারির গতিবিধি নিরীক্ষণ করছিল। ভাগ্য ভাল, প্রভুরা সেদিনকার মতো জিপে উঠে চলে গেল। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।
পরদিন ১৫ই ডিসেম্বর। সেদিন ওদের আর আসতে হয়নি। ছেলেরা ‘জয় বাংলা’ রব তুলে আকাশ বাতাস ভরিয়ে ফেললো। আনন্দে উৎফুল্ল লোক দলে দলে ছুটলো আঠারো নম্বর রোডে ঐ লাল বাড়িটায় বন্দী ‘আস্লী চিড়িয়াদের’ মুক্ত হতে দেখবে বলে। আমরা ভাবলাম, স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগটা আগে তুলে নিই, তারপর ধীরেসুস্থে যাবো, এই পরের রাস্তাটাই তো! এত তাড়া কিসের! ছাড়া পেলে রেহানা নিজেই আসবে শুক্লার কাছে। ওমা, একি বাগড়া বাধলো আবার? ডা. আছিরুদ্দিন সাহেবের ছেলে ওদের ছাদ থেকে হেঁকে বলছে, ‘অ্যাই, ফ্ল্যাগ নামাও। ও পাশের সেপাই-সান্ত্রীরা ক্ষেপে উঠেছে, ফ্ল্যাগ টাঙাতে দিচ্ছে না। ওরা এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ছে।’ গুটিকতক পাহারাদারের আস্পর্ধা! যুদ্ধ থেমে গেছে, নিয়াজী কাল সারেন্ডার করবে বেলা চারটেয়, ওনাদের আবার এত তেজ! বাস্তবিকই ওরা কিছুতেই যুদ্ধবিরতি মানতে রাজি নয়। ঐ রাস্তাটার মোড়ে রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধেছে। দুপাশের বাড়িঘরগুলো গোলাগুলির চোটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। বেশ কিছু নিরীহ পথচারী হতাহত। ঐ লালবাড়িটার উল্টো দিকের বাড়িতে ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধা জড় হয়েছে, এরা কিছুতেই এগুতে পারছে না। এদিকে রেডিওতে তখনো প্রচার করা হচ্ছে নিয়াজীর আসন্ন আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের খবর। রেসকোর্সের ময়দানের বৈঠকের খবর এমন বহুলপ্রচারিত সর্বত্র সাড়া জাগিয়েছে, আর কি আশ্চর্য, ঐ ক’টা খান সেনার কাছে তা পৌঁছানো যাচ্ছে না! তারা দারুণ মরিয়া, মারমুখো হয়ে উঠেছে। অগত্যা জেনারেল আরোরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে খালি দুহাত উঁচিয়ে ওদের এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন ওদের। সবই হলো, মাঝখান থেকে কতগুলো মূল্যবান প্রাণ হারিয়ে গেল। বেলা দুটোর দিকে আমরা নির্ভয়ে ফ্ল্যাগটা তুলে মনের মধ্যে কতদিনের কবর দেওয়া সাধ পূর্ণ করলাম।
এখানেই খুনোখুনি শেষ হলো না। নিয়াজীর আত্মসমর্পণ নিজের চোখে দেখতে গিয়েছিল অনেক লোক। দুশমনদের ভেতরে হিংসার আগুন তখনো নেভেনি। ‘যেতেই যখন হবে, আরো কিছু মেরে রেখে যাই’, এই মনোভাব নিয়ে সুযোগমত গুলি চালাতে কসুর করেনি ওরা। আমার এক সহকর্মী, অঙ্কের প্রফেসর, এর স্বামী এদের শিকার হয়ে একখানা পা হারালো বুলেট লেগে। অনেকের মাঝে এ মাত্র একজন, এমনি আরো কতজনের অকারণ ক্ষতি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নয়টি মাসের সব আতঙ্ক, উদ্বেগ, হয়রানি, ক্ষয়ক্ষতি পার হয়ে এসেও এগুলো উপরন্তু দণ্ডি গেল। কী পরিতাপের বিষয়!
কথা শেষ হয়েও কিছু বাকি রয়ে যায়, তাই ক্যাপ্টেন ফারুকের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসতে হয়। যা-ই বলি না কেন, ক্যাপ্টেন সাহেব কিন্তু নেহাৎ নিমকহারাম ছিলেন না। ঘোরতর কারফিউয়ের সময় আমাদের যখন দুবেলা আলুভাতে ভাত জোটানো দুষ্কর ছিল তখন পৃষ্ঠপোষকদের নিয়মিত মুরগি-মটন বাজার এসেছে সেপাই মারফৎ। যাবার বেলায় তাদের জন্যে অনেক দামী দামী উপহার-মোটরকার, রেডিও, টেলিভিশন, কার্পেট, ফোম-ম্যাট্রেস ইত্যাদি দিয়ে গেছে। কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন, এত সব কোথেকে এলো? মাল-এ-গণিমত হয়ত!
আমরা প্রতিবেশীরা দেখেও দেখিনি। পাছে চোখে চোখ পড়ে যায়, চোখ বুজে রেখেছি সময়মত। ঐ যে কথায় বলে না, ‘বান্দার মার তড়িঘড়ি, আল্লাহর মার রয়ে সয়ে।’ আমরা যতই চোখ বুজে থাকি না কেন, মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের চোখকান সজাগ ছিল। ঠিক স্বাধীনতার দিন, ১৬ই ডিসেম্বর, দল বেঁধে এসে সেই সব বাড়ি ঘেরাও করেছিল। তখন যত হাবা-কালা-বোবা প্রতিবেশীরাই অনেক অনুনয় করে তাদের নিরস্ত করেছে, আজকের দিনটা আর খুনখারাবি নয়, এদিনের পবিত্রতা রক্ষার জন্যেই ওদের রেহাই দেওয়া হলো। লজ্জা থাকলে জীবনে ওরা আর এমন আচরণ করবে না।
স্বাধীনতার পরদিন, ১৭ই ডিসেম্বর সকালে বেশ খুশি খুশি ভাব, নিশ্চিন্ত মনে ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি, হঠাৎ বেলা দশটা সাড়ে দশটার দিকে আমার বান্ধবী আছিয়ার ভাই আবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। গেটের বাইরে থেকেই, ‘আপায় কই? আমার আপায় কেমুন আছে?’ বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে হড়বড় করে দৌড়ে উঠে আসছে। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে বললো, ‘ভালোই আছেন। আপনি বসুন, আম্মাকে ডাকছি।’ সে অস্থিরভাবে বলে, ‘না, আগে আপারে দেইখা লই।’ ততক্ষণে আমি বেরিয়েছি। আমাকে দেখেই আবু জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ধপাস করে মেঝেতেই বসে পড়লো। পরে একটু সুস্থির হয়ে ঘরে এসে বসলো। তখনো থর থর করে কাঁপছে। ‘আয় হায়! আমি বুঝছি কি, আমার আপায় বুঝি আর নাই।’… ও এসেছে রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে আল্বদরদের লীলাখেলা দেখে। বহু লাশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে, তখনো শনাক্ত হয়নি। তাদের মধ্যে একটিকে ওর কাছে আমার মতো লেগেছে। পরে জানলাম, সে হচ্ছে মহিলা সাংবাদিক সেলিনা পারভীন। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এমনি অনেক ঘটনা জানতে জানতে বেশ অনেক দিন লেগেছিল হিসেব মেলাতে।
উৎস : রচনা সংগ্রহ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪।




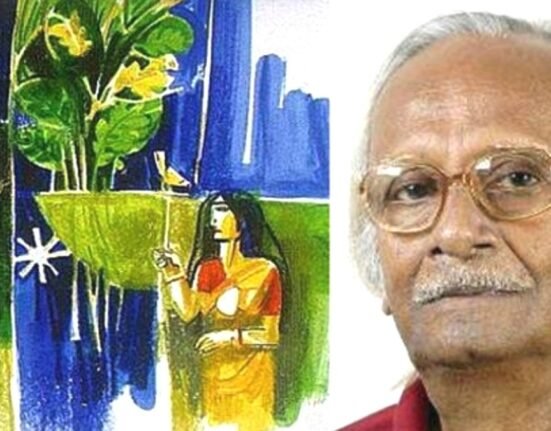

Leave feedback about this