তীরন্দাজ নববর্ষ সংখ্যা
‘নব বৎসরে করিলাম পণ, লব স্বদেশের দীক্ষা।’ তাহলে তো শুরুতে একটা প্রশ্ন, আমাদের নববর্ষ কবে? স্বদেশের দীক্ষা নেওয়ার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তা, সেই স্বদেশের নববর্ষ কবে, সেটা তো জানা চাই।
আমাদের দেশে অনেকগুলি নববর্ষের দিন আছে। ইংরেজি নববর্ষকে না গুনেই বলছি একথা। অনেক নববর্ষ, কোনটা যে মানা উচিত, স্বদেশের বলে গণ্য করা উচিত, বোঝা কঠিন। প্রায় প্রতিমাসেই একটি করে নববর্ষ আছে এই দেশে। বঙ্গাব্দ আছে, শকাব্দ আছে, বিক্রমাব্দ আছে। এমন আরও অনেক নববর্ষের কথাও জানা যায়।
ধরা যাক আদিবাসীদের কথা। তারা থাকতেন গভীর জঙ্গলে। বিদ্যুৎ বলে কিছু তখন ছিল তো নাই-ই, কেরোসিন বা গ্যাসের কথাও ভাবা যেত না। সারাদিনের কর্মক্লান্ত মানুষগুলি আরও অতীতে কাঠের আগুনে শিকার করে আনা জীবজন্তু পুড়িয়ে, ঝলসে তার মাংস খেতেন। অন্ধকার ঘন হলে জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে গুহার মুখে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে ঘুমোতেন। রাতে তাদের আনন্দের অবকাশ ছিল শুধু পূর্ণিমার আগে ও পরে মিলিয়ে দিন তিনেক। প্রতিমাসের পূর্ণিমাতে তাই আদিবাসীদের উৎসব। সেই সব উৎসবই আমরা, যারা নিজেদের ‘সভ্য’ বলে দাবি করি, তারা আত্মস্থ করেছি। সেগুলিই নানা এলাকায় নানা নামে আজও পালিত হয়। প্রকৃতির সেই সব উৎসবের সঙ্গে দেবদেবীদের জুড়ে দেওয়া অনেক পরের কাহিনি। মূল উৎসবগুলি ছিল বাহা, বিহু, সহরুল, স্যালসেই, পোঙ্গল, ওন্নাম, বিজু ইত্যাদি। তেমনই এসেছে চৈতি, বিরহা, লোরি, গুডি পরব, কড়েয়া চৌথ ইত্যাদি। কত যে নাম নববর্ষের আনন্দ উৎসবের!
অনেকেই বলে থাকেন, পয়লা বৈশাখের বঙ্গাব্দের নববর্ষ পালন শুরু হয়েছিল মুঘল আমলে। মুঘল সম্রাট আকবর খাজনা আদায়ের জন্য ফসলি মাস শুরু করেছিলেন পয়লা বৈশাখ থেকে। সেদিন আগের বছরের ফসলের বকেয়া দিয়ে পরের বছর শুরু করা হতো। এটাই পরে আমাদের কাছে ‘হালখাতা’ হয়ে এসেছে।
কিন্তু তার আগে কী নতুন বছর বলে কিছু ছিল না? বছরের শুরুর একটি দিন তো নিশ্চয়ই ছিল! অন্তত থাকার কথা, তাই না?
এখানেই একটা বড় বিস্ময় মহাকাশের কালপুরুষের মতো বিশাল প্রশ্নচিহ্ন হয়ে মনের আকাশে ঝুলে আছে। আমিনুর রহমান সুলতান বলেছেন, ‘রাজা শশাঙ্কর সময় থেকে আকবরের আমল পর্যন্ত নববর্ষ পালনের কোনও নজির পাওয়া যায় না।’ হতেই পারে, হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই বলে বছরের শুরু নেই, শেষ নেই, হয় এটা? ইউরোপে যেমন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়, আমাদের দেশে সেভাবে ইতিহাস লিখিত আকারে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, সেগুলি পুরাণ বা উপনিষদের নানা গল্প কাহিনি, কল্পকথা।
কিন্তু কটকের রাভেনশ কলেজ, প্রেসিডেন্সি ও চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, যিনি অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক বই রচনা ছাড়াও গণিত, জ্যোতিষ, জ্যোতিবির্দ্যার সাধন, বাংলা শব্দকোষ প্রণয়ন করেছেন; তিনি দারুণ একটি তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। বলেছেন, বহু শত বছর আগে আমাদের দেশে ৩৬৫ দিনে একটি নয়, দুটি বছর গণনা হতো। অর্থাৎ, ছয় মাসে এক বছর গণনা হতো। ৩৬৫ দিনে এই দুটি বছরের নাম ছিল হিমবর্ষ ও শরৎ বর্ষ। ঋতুও ছিল দুটি – শরৎ আর হিম ঋতু।
হিম বর্ষের শুরু হতো অগ্রহায়ণে, শরৎ বর্ষের শুরু জৈষ্ঠ্য মাসে। মাসের নামগুলিও তারই সাক্ষ্য দেয়। জেষ্ঠ্য অর্থাৎ প্রথম। প্রথম মাস বলেই সে জৈষ্ঠ্য। শরৎ ঋতুর ও শারদ বর্ষের শুরু অগ্রহায়ণে। আর ‘অগ্র’ অর্থাৎ আগে। ‘আয়ন’ অর্থাৎ সূর্যের গতি, যেমন সূর্যের উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন। প্রথম আয়ন হিসাবে অগ্রহায়ন।
অগ্রহায়ণ মাস হিন্দুদের কাছে নল রাজার পুণরায় রাজ্যাভিষেকের মাস আর সারনা ধর্মের অনুসারীদের কাছে বাঁধনা পরবের সময়। এটি হিমবর্ষের নববর্ষ মাস।
পুরাণের যুগে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর সাঁওতাল, খেড়িয়া, শবররা থাকতেন তাদের রাজ্য চম্পানগরে। হিন্দুদের যেমন যমরাজ, খেরওয়াল আদিবাসীদের মৃত্যুর দেবতার নাম হুদুলরাজ। তিনি ‘মরণ’ রাজ্যের রাজা। মরণ রাজ্যকেই আমরা পাতাল বা নরক বলি। আদিবাসীদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর মানুষ প্রথমে যায় ‘হানাপুরী’ বা অন্যলোকে। সেখানে বিচারের পর ভালো মানুষরা যায় ‘সেরমাপুরী’ বা স্বর্গলোক; আর বাকিরা মরণ বা পাতাল নরকে। জীবিত কোনও মানুষ মরণ রাজ্যে যেতে পারেন না।
মরণের রাজা হুদুলরাজ কঠোর হাতে রাজ্য সামলান। তাঁর নিয়ম বদলায় না। কিন্তু, একবারই তাকেও নিয়ম বদলাতে হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই সাঁওতাল ও আদিবাসী সমাজে ‘সরহুল’ উৎসবের শুরু। কারও কারও মতে এর অপর নাম স্যালসেই উৎসব। সরহুল উৎসবের সমাপ্তিতে হয় স্যালসেই। আদিবাসী সাহিত্য সংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক ড. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে সরহুলের সেই কাহিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন।
খেরওয়াল জাতির প্রাচীন প্রবাদ, বিশ্বের মাতার নাম ধরিত্রী। বিন্দি তাঁর মেয়ে। ধরিত্রীই সব প্রাণের উৎস, ফসলের জন্মদাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী। তাই তিনি প্রাণেরও দেবী। নয়ণমণি কন্যা বিন্দিকে তিনি সবসময় চোখে চোখে রাখেন। কিছুক্ষণ চোখের আড়াল হলেই অস্থির হয়ে যান। কিশোরী বিন্দি খেলে ফুলবাগিচায়, ফলের বনে, ছবির মতো সুন্দর স্রোতস্বিনী নদীর পাশে।
একদিন বিন্দি একাই নদীতে স্নান করতে গিয়ে আর ফিরছে না। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে পার হয়ে রাত হলো। বিন্দি ফিরল না। মা ধরিত্রী অস্থির হয়ে উঠলেন। সর্বত্র খুঁজেও বিন্দিকে পাওয়া গেল না। উতলা ধরিত্রী তখন বলতে থাকলেন, ‘বিন্দিকে না পাওয়া গেলে এ জীবনই আর রাখব না। কার জন্যে বাঁচব!’ তিনি তাঁর স্বাভাবিক সব কাজ বন্ধ করলেন। ধরিত্রীদেবী স্থানু হয়ে অনশনে বসলেন, সব ফসল শুকিয়ে গেল। গাছের পাতারা হলুদ হয়ে ঝরে গেল। বাগানের ফুল, বনের ফল, শুকিয়ে মরে গেল। মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এল পৃথিবীর বুকে। এই বুঝি পৃথিবী রসাতলে যায়!
দেবতারা প্রমাদ গুনলেন। পৃথিবীই তো ধরিত্রী। সে যদি মারা যায়, কারোরই বেঁচে থাকার উপায় থাকবে না। আর মানুষই যদি না বাঁচে, দেবতারা কাদের নিয়ে সংসার চালাবেন! তখনকার দিনে আদিবাসীদের সব দেবদেবীই প্রকৃতির পূজক। প্রকৃতিকে বাঁচাতে তাঁরা ও ধরিত্রীর অনুচরেরা বিন্দিকে খুঁজতে খুঁজতে এলেন হুদুলরাজের প্রাসাদে। জানতে পারলেন, বিন্দি রয়েছে সেখানেই। তারা হুদুলের কাছে গিয়ে বিন্দির মুক্তির জন্য আবেদন জানালেন। কিন্তু হুদুল নিয়মের বাইরে গিয়ে কিছু করেন না। তার রাজ্যে নিয়ম ভাঙার কোনও উপায়ই নেই। আইন অমান্য হয় না। হুদুল বললেন, ‘অসম্ভব। মরণরাজ্যে একবার কেউ এলে তার আর ফিরে যাওয়ার কোনও নিয়ম নেই। নিয়ম ভাঙারও কোনও উপায় নেই। বিন্দির ক্ষেত্রেও সেটাই মানতে হবে।
অনুচরেরা সবিস্তারে জানালেন, বিন্দির শোকে মা ধরিত্রীদেবী পাথর হয়ে গেছেন। অনশনে বসায় মৃত্যু গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করছে। তাই বিন্দিকে যেন তিনি ফিরে যেতে অনুমতি দেন। তাদের বারংবার অনুরোধেও চিড়ে ভিজছে না। হুদুলরাজ অনড়। অবশেষে তাঁরা প্রয়োগ করলেন ব্রহ্মাস্ত্র। বললেন, ‘বিন্দির বিহনে ধরিত্রীমাতা স্নান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝড়ে যাচ্ছে, ফুল ফল মরে যাচ্ছে। পৃথিবীর রং বদলে গেছে। ধরিত্রীমাতা আত্মহত্যা করলে সৃষ্টিই থাকবে না। যদি সৃষ্টিই না থাকে, হুদুলই বা কার উপর রাজত্ব করবেন!
হুদুলরাজ এবার চিন্তায় পড়লেন। খানিক ঘাবড়ালেনও। এও তো সত্যি! সৃষ্টিই যদি না থাকে, সবার অস্তিত্বই শেষ! সেক্ষেত্রে সব দোষ তখন আসবে তাঁরই ঘাড়ে! কিন্তু, বিন্দিকে তো তিনি ইতিমধ্যে মরণের রাণি করে দিয়েছেন। তার কী হবে? রাজ্য থাকবে, রাজা থাকবেন, প্রজারা থাকবে, কিন্তু রাণি চলে যাবেন, এটাই বা হয় কী করে? প্রজারা রাজার ছিঃ ছিঃ করবে যে!
সাত-পাঁচ ভেবে দেবতাদের জন্য শর্ত দিলেন হুদুল। বিন্দি যেহেতু জীবিত অবস্থায় মরণ রাজ্যে এসেছিল, তাই তাঁকে এখন মায়ের কাছে ফিরে যেতে দেবেন। কিন্তু, যেহেতু বিন্দি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছিল এবং তাঁকে রানি করা হয়েছে, তাই বছরের একটা সময় তাকে এখানে এসে কয়েক মাস থাকতে হবে। ধরিত্রীর অনুচরদের কাছে তখন বিন্দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ধরিত্রীকে বাঁচানোই প্রধান বিষয়। বাকি সব শর্ত মানা যাবে, আগে ধরিত্রী বাঁচুন।
তাঁরা রাজী হলেন। বিন্দিও নাচতে নাচতে ফিরে এল মায়ের কোলে। আবার ফুলে ফুলে ভরে গেল পৃথিবী। গাছে গাছে সবুজ কচি পাতারা ছেয়ে গেল। শুরু হলো কলকণ্ঠের কাকলি। ফুলের বর্ণে, গন্ধে মন ভরে গেল বিশ্ববাসীর। তারা উৎসবে মেতে উঠলেন। যতদিন ধরিত্রী অনশনে ছিলেন, পৃথিবীতে নেমে এসেছিল শীত। বিন্দি ফিরে আসায় এল বসন্ত। এল বসন্তের উৎসব।
পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেছেন, ‘প্রাচীনকালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নববর্ষের উৎসব হতো। দোলযাত্রা সেই উৎসবেরই স্মারক।’ এই উৎসবটাই আদিবাসীদের প্রিয় ফুলের উৎসব ‘বাহা’ বা বসন্তের ‘সরহুল’। এর শুরু হয় মাঘ মাসে, যখন ফুলে-ফুলে গাছপালা ভরে যায়। আর এর শেষ হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাতে। সেই রাতের দিনের উৎসবের নাম স্যালসেই। সেইদিন খেরওয়াল জাতির নববর্ষ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসবের বদলে বোলপুরের আদিবাসী সমাজের সেই নাচ-গানের উৎসবকেই শান্তিনিকেতনে ‘বসন্ত উৎসব’ বলে চালু করেছিলেন। যখন নীল দিগন্তে ফুলের আগুন লাগে। ও চাঁদ লাগায় দোলা। কবি গেয়ে ওঠেন, খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল, স্থলে জলে বনতলে লাগলো যে দোল, দ্বার খোল, দ্বার খোল’। যৌবনের নবীন বর্ষের সূচনা বুঝি করে গিয়েছিলেন এভাবেই।
নববর্ষ মানেই আসলে আনন্দের নানা রঙের সুতোয় গাঁথা। যেদিনই আনন্দ, সে দিনটাই নববর্ষ নয় কেন?


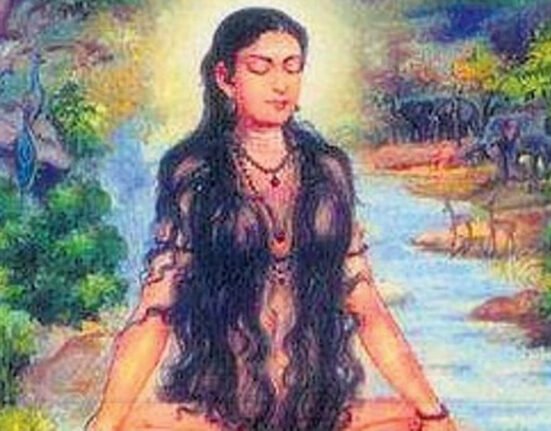


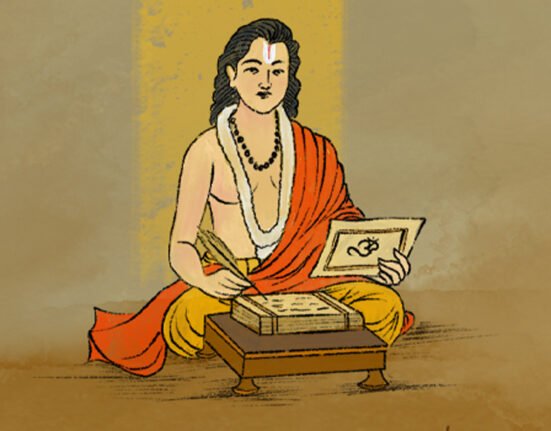

Leave feedback about this