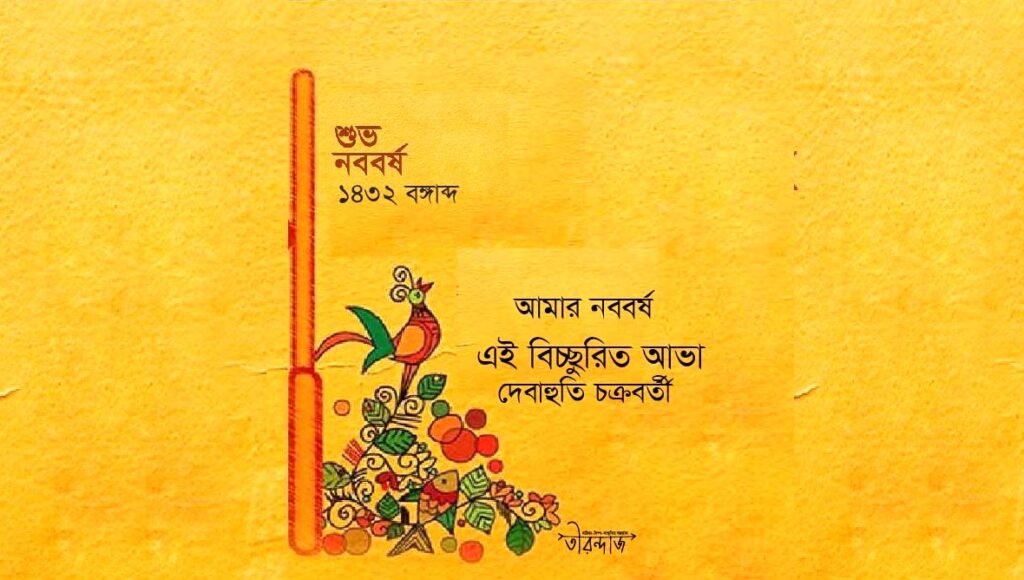তীরন্দাজ নববর্ষ সংখ্যা
আমার নববর্ষ? বিশেষ একটা দিন কিন্তু বিশেষ একটা সনের নয়। সাত দশক পার করা জীবনে নববর্ষের আসা-যাওয়ার বয়সও যথেষ্টই দীর্ঘ। তবে খুব বেশি বৈচিত্রপূর্ণ নয়। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক বাঁক নিয়েছে, এইটুকুই।
শৈশবের দিকে ফিরে তাকাই। আমার জন্মস্থান রাজবাড়ী। এখন জেলা শহর। একসময় গ্রাম আর শহরে মাখামাখি করা মফস্বল। ছোটবেলায় বাড়ির সীমানায় দাঁড়িয়ে চারপাশে যতদূর দেখা যেত, সবটাই জানতাম বাড়িরই সীমানা। এখন সেখানে ভগ্নপ্রায় একটা পুরানো বিল্ডিং ছাড়া বড়সড় একটা লোকালয় গড়ে উঠেছে। আমার নববর্ষ মূলত বাড়ির সীমানা ঘিরেই আবর্তিত ছিল। আশেপাশের সব ধর্ম-বর্ণের, সব শ্রেণি-পেশার সব বয়সী মানুষের আসা-যাওয়া ছিল বাড়িতে। উৎসব আনন্দের বেশিটাই ভাগাভাগি হয়ে যেত এখানেই। বাড়ির আশেপাশে হিন্দু পরিবারই ছিল বেশি। দু-চারটে মুসলিম ঘর।
অন্য সব কিছুর মতো হিন্দু পরিবারগুলোয় নববর্ষেও আচার-অনুষ্ঠান বেশি ছিল। চৈত্র সংক্রান্তি পালন আর বর্ষবরণের আয়োজনের মাঝে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র ছিল। পুরাতনকে বিদায় আর নতুনকে আবাহন দুইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট সংযোগ ছিল। মধ্য চৈত্র থেকে পাটঠাকুর মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরা, নীল পুজো, ছিন্নমস্তা শ্মশান কালী পুজো, চড়ক উৎসব, চড়কের আগে দলে দলে মুখোশ নৃত্য, সঙ সেজে অভিনয়, অষ্টক গান, ভৈরব সাধুর কয়েকদিনের শ্মশান মেলা এই নিয়ে চারদিক নানা সমারোহে মেতে উঠত।অধিকাংশ আচার-আয়োজন ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। মুসলমানরাও অনেকক্ষেত্রে অংশ নিত। বিশেষ করে আমার দেখামতে অষ্টক গানের দল ছিল কাহার সম্প্রদায়ের মুসলমানদের পরিচালিত। তারা দিনে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। রাতে সেজেগুজে নূপুর ঝমঝম করে বাজিয়ে হ্যাজাক আলো হাতে নিয়ে এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরে নাচ গান পুরাণভিত্তিক পালা অভিনয় করত। অবসর বেশি থাকলে সঙ সেজেও বখশিশ তুলত। এ নিয়ে কোনো সম্প্রদায়ের কোনো উচ্চবাচ্য কোনদিন শুনিনি। আর মেলায়, মেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিম সম্প্রদায় নির্দ্বিধায় অংশ নিত। এ সময় সবার মধ্যেই চৈতালি ফসল ঘরে তোলার একটা বিষয় ছিল। এসব ব্যস্ততার মাঝে হিন্দু পরিবারে বর্ষবরণ নিয়ে আলাদা একটা ব্যস্ততা ছিল। যার যেমন বাড়ি-ঘর, যার যেমন আসবাবপত্র – ঘরের নিত্যদিনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র, জামা কাপড় সব ঝাড়াপোঁছা, ধোওয়া-কাচা করাটাই নিয়ম ছিল। বছর ভরে ঘরে জমে ওঠা যা কিছু আবর্জনা, যা কিছু অতিরিক্ত, তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করায় হিন্দুরা পারদর্শী ছিল। বলাবাহুল্য শুচি শুদ্ধ পরিবেশে নতুন বরণের এই অমানবিক পরিশ্রম বাড়ির বিভিন্ন বয়সী মেয়েদের সামলাতে হতো। তুলনামূলকভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিবারগুলোয় এমন প্রাণান্তকর পরিশ্রম কম ছিল।
বৈশাখের প্রথম দিনে উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হালখাতা নববর্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পুরানো হিসাবনিকাশ, দেনাপাওনা হাল নাগাদ করা মিষ্টিমুখ করার মাঝ দিয়ে ক্রেতা- বিক্রেতার সম্পর্কের একটা ঝালাই হতো। হালখাতা এখনো আছে। তবে অনেকেই নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী যে কোনো সময় বেছে নেয়। ছোট-বড় সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেই হিন্দুদের বিশেষ পুজো হতো। যেমনটা হতো প্রত্যেক বাড়িতে। সকালে স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন পোশাকে পুজোর ঘর থেকে শুরু করে বাড়ি এবং আশেপাশের বাড়ির বড়দের প্রণাম করা নিয়মের মধ্যে ছিল। বছরের প্রথম দিন থেকে মাসব্যাপী হিন্দুরা তুলসীগাছ খররোদ থেকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ কায়দায় ঝোরা বাঁধত। সারাসময় ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ত গাছের ওপর। এই তুলসী ভিটাতেই সব বাড়িতে সন্ধ্যায় সংকীর্তন করে বাতাসা ছিটিয়ে হরিলুট দেওয়া হতো। বাতাসা সংগ্রহের সবার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা ছিল। ভোর না হতে মাসব্যাপী চলত টহল বা প্রভাতী গান। খোল করতাল নিয়ে সমবেত সুর শোনা যেত – ‘ভোর হইল, জগত জাগিল, চেতনে চাহিল নারী নর’; আমাদের বিছানা ছাড়তে হতো।
বৈশাখের প্রথম দিন সব সম্প্রদায়ের বাড়িতে সাধ্যমতো উন্নত খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হতো। মিষ্টি জাতীয় কিছু থাকবেই। দিনভর অতিথি আপ্যায়নের জন্য ছাতু, খই, মুড়ি, চিড়া, দৈ, দেশজ ফল-ফলারির আয়োজন থাকতই। পান্তা ভাত, ভর্তা, ইলিশ মাছ অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল না। পান্তা জোটাতে অনেক পরিবারই হররোজ হিমশিম খেতো। নতুন জামাকাপড়ের তেমন চল ছিল না। হিন্দু মুসলিম সব বন্ধুই একে অন্যকে ফুল উপহার দিত। উপহারের ফুল বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে কে কতদিন সযত্নে শুকিয়ে রাখতে পারে, তার একটা প্রতিযোগিতা ছিল। কিছুটা বড় হলে ফুলের সাথে কার্ড দেওয়া নেওয়া চালু হয়েছিল। কার্ড কেনার কথা আমাদের ভাবনার মধ্যেও ছিল না। হাতেই যে যার মতো সুন্দর করে কার্ড বানিয়ে শুভেচ্ছাবাণী বিনিময় হতো। এর জন্য প্রস্তুতি চৈত্র সংক্রান্তি থেকেই নিতে হতো। বৈশাখের প্রথম দিনটা পার হওয়া মানেই নববর্ষ বরণ শেষ হওয়া নয়। বিজয়া পরবর্তী দায়িত্বের মতই আর একটা দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক ছিল। আত্মীয় পরিজন, শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে রীতিনীতি মেনে পোস্টকার্ড বা এনভেলাপে পত্র লেখা। শুদ্ধমত হয়েছে কি না, তা নিয়ে মায়ের খবরদারি ছিল। এই অধ্যায়গুলো একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। চিঠি দেওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ পেতাম, তার অভাব এখনো অনুভব করি।
আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন উপমহাদেশখ্যাত জলতরঙ্গ শিল্পী বামন দাশ গুহরায়। শুধু জলতরঙ্গ নয়, সব রকমের বাদ্যযন্ত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়ে তাঁর কাছ থেকে তালিম নেওয়া হিন্দু-মুসলিম ছেলেমেয়েরা রাজবাড়ীকে সব সময়ই জাতীয় স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। আমৃত্যু নববর্ষ উপলক্ষে তাঁর পরিচালিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমরা দেখেছি, অংশ নিয়েছি। বৈশাখের বড় মেলা বসতো লক্ষ্মীকোল রাজবাড়ী এলাকায়। বুড়ির মেলা নামে খ্যাত এই মেলা ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় এলাকায় মেলা, লাঠিখেলা, যাত্রা, কবিগান হতো। সব সম্প্রদায়ের সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণে সেসব অনুষ্ঠান অনেক আকর্ষণীয় ছিল সবার কাছে।
কৈশোর পেরোতেই আমাদের এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দটা অনেকটাই কমে আসতে থাকে। রাজবাড়ী নদীভাঙন আর বন্যায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকা। জায়গা জমি তুলনামূলক সস্তা। বিভিন্ন জেলার মানুষ কিছু জমি কিনে অজ পাড়া গাঁ থেকে মফস্বল অবধি আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। ব্যতিক্রমী কিছু মানুষ বাদে এই আধিপত্যের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা সুস্পষ্ট দানা বাঁধতে থেকে। চৈত্রসংক্রান্তি আর বর্ষবরণ অনুষ্ঠান থেকে সাধারণ মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। তবে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ষাটের দশক থেকে বিপরীত এক শক্তির ক্রম উত্তরন ঘটতে থাকে। অপেক্ষাকৃত তরুণ আর প্রগতিশীলদের নেতৃত্বে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সর্বজনীন হতে থাকে। সেসব আয়োজনে আড়ম্বরের বাহুল্য না থাকলেও উৎসাহ আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল না। সচেতন বা অচেতনভাবেই সেইসব সাংস্কৃতিক লড়াই দেশব্যাপী চলতে থাকে এবং তা রাজনৈতিক লড়াইকে বিকশিত হতে নিরবচ্ছিন্ন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যার ক্রম এবং পূর্ণ বিকশিত রূপ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই আবার স্পষ্ট হতে থাকে যে, বাঙালি মুসলমানের জাতিগত আত্মপরিচয়ের সংকট রয়েই গেছে। চুয়ান্ন বছর ধরে নববর্ষ পালনের উৎসব অনুষ্ঠানে যথেষ্ট অংশ নিয়েছি। আবার চুয়ান্ন বছর ধরেই দেখে এসেছি সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের ডালপালা বিস্তার। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা নানাভাবে সংকটের মুখে পড়েছে। নববর্ষ এখন আর উদার আকাশের নিচে উন্মুক্ত মনুষ্যত্ব বিকাশের আনন্দ নয়। ‘আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম’ – গানটা এখন বেশি বেশি মনে হয়।
সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে ছোট থেকেই বিপন্নতা বোধ আমাদের ছাড়েনি। রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রযন্ত্রের নানা চাপের মাঝে টিকে থাকার লড়াই বজায় রাখতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিদিনের সামাজিক জীবনে ধর্মীয় হিংসা বিভেদ বিদ্বেষ কখনো প্রকট ছিল না। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বাদে নববর্ষ কখনো আমার ছিল না, একান্তই আমাদের ছিল। জীবনসায়াহ্নে এসে সেই সামাজিক নৈকট্যের মধ্যে ফাঁক আর ফাঁকিটা মনকে পীড়িত করে। একুশ শতকের দুই দশক পেরিয়ে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের দিনে আমরা নববর্ষ নিয়ে নানা তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কারে ব্যস্ত ও ব্যগ্র হয়ে উঠেছি। নববর্ষ পালনের মাঙ্গলিক সুরটা কোথায় যেন কেটে গেছে। দেশের সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক অকৃত্রিম উৎসব আজ নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। অনেক উত্তরই আজ মেলানোর নয়। আরও দূরপথ সামনে অতিক্রমণের। আমার সামনে এখন নতুন বছর মানেই জীবন থেকে সংসার থেকে সময় থেকে আরও পুরাতন হওয়া। এটা প্রকৃতির নিয়ম। অমীমাংসিত কোনো বিষয়কে বাইরের আবরণ দিয়ে আর আড়ম্বর দিয়ে দীর্ঘদিন ঢেকে রাখা যায় না, এটাও প্রকৃতির নিয়ম। সেটা যত সহজে উপলব্ধি করা যায়, ততই সবার জন্য ভালো। বিপন্নবোধ থেকে মনকে সজীব রাখা যায়।
অপার্থিব জীবনের চাওয়া পাওয়ার তাড়না কোনোদিনই আমার নেই। তাই বলতে পারি, বাংলা নববর্ষ আমার প্রধানতম উৎসব। যার মর্মবাণী দেওয়া আর নেওয়া, মেলা আর মেলানো। নববর্ষের মূল সুর হারানো মানে আমার অনেকটাই হারানো। কয়েক বছর আগে নববর্ষের একটা দিন মৃতপ্রায় আমি টাটা মেমোরিয়ালের উদ্দেশে সকালের উড়ানে মুম্বাইয়ের পথে ছিলাম। তখনও মনে হচ্ছিল – ‘আজ আমার বাংলাদেশের নববর্ষের প্রথম প্রভাত। সারা দেশ জেগে উঠছে নব আনন্দে, নব আয়োজনে। আমার জন্য আজ এ কোন আয়োজন? নববর্ষের নবপ্রভাতকে আমি কীভাবে বরণ করছি? শুভ নববর্ষ দুটো ছোট শব্দ। এর মাঝে রয়েছে আমার সারা বছরের পথচলার প্রেরণা আর শক্তি। শব্দ দুটো কারো সাথে বিনিময় হওয়ার কোনো সুযোগ আজ নেই। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণায় ঝাপসা হয়ে আসছে সবকিছু। তবু অনুভব করছি দেশের মাটিতে প্রথম সূর্যোদয়কে। প্রথম ঊষার এই বিচ্ছুরিত আভা রাতের অন্ধকারকে দূর করে জ্যোতির্ময় দিনের দিক এগিয়ে যাবে নবপ্রভাতের এই তো চাওয়া।’ সেই চাওয়াটুকু আজও রইল।